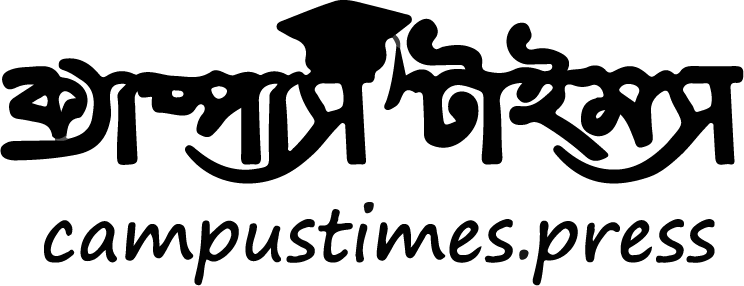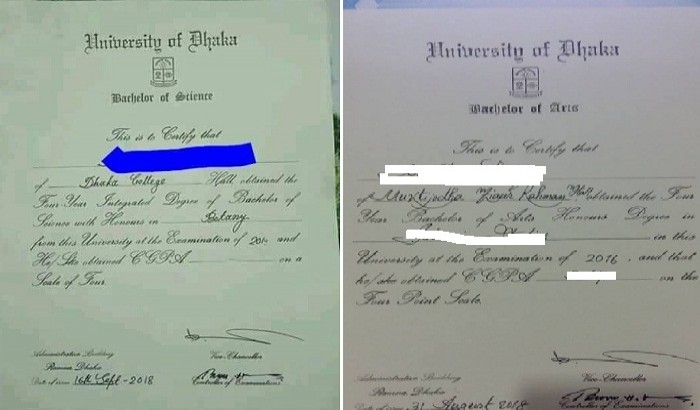বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯২১ সালের ১ জুলাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি দিন। বিশেষ করে বাঙালির আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা এদিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তথা Dacca University Act, 1920 (Act XVII of 1920) নীতিগতভাবে সহ-শিক্ষার বিষয়টি স্বীকৃত ছিল। সেটা ওই সময়ের জন্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । সেই আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছিল যে be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class...’’ । অবশ্য যখন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার জন্যই উন্মুক্ত থাকবে, এবং তা হবে একটি শিক্ষাদানমূলক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। [Dacca University]... ‘would be a University open to all-a teaching and a residential University’.
পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির কথা প্রায়ই বলা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুরু থেকেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ; এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পূর্ব বাংলার সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন গ্রামীণ মুসলমান মধ্যবিত্ত, সম্পন্ন কৃষক ও নিন্মবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে ২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলায় একটি নতুন হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছিল, যারা শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশকের মধ্যে পূর্ব বাংলায় একটি আলোকিত আধুনিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।সেই অবস্থায় ৯৯ বছর আগে ঢাকার মতো একটি অবহেলিত ও অনগ্রসর প্রাচীন নগরীতে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ।
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিয়োগ । শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা উভয় ক্ষেত্রেই স্যার ফিলিপ হার্টগ ছিলেন অসাধারণ। তাঁর সময়ের সবচেয়ে আধুনিক শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক রেজিস্ট্রার ছিলেন প্রায় ১৭ বছর। সেই পদে থাকাকালে তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ম্যানচেস্টার বা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথাগত চাকরি করেননি। পূর্ববাংলার মানুষের সৌভাগ্য যে তিনি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশাল সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর পাঁচ বছরের প্রশাসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ভারতবর্ষের নয়, কমনওয়েলথ দেশগুলোর মধ্যে একটি বিশিষ্ট উচ্চ মানসম্পন্ন বিদ্যাপীঠের স্বীকৃতি পায়। ধর্মীয় পরিচয়ে তিনি ছিলেন একজন ইহুদি, জাতিতে ব্রিটিশ। সে বিচারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা অসাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল ।
দুই.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বহুল প্রচলিত দু’টি মিথের অবসান হওয়া জরুরি। একটি হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধ ছিলেন বলে একটা কথা বেশ কিছুকাল ধরে বাংলাদেশে মুখে মুখে চলছে। কেউ কেউ কোনো প্রমাণ উপস্থিত না করেই লিখিতভাবে জানাচ্ছেন যে, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। ও রকম একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল অসম্ভব, কেননা সেদিন তিনি কলকাতাতেই ছিলেন না। ১৯১২ সালের ১৯ মার্চ সিটি অব প্যারিস জাহাজযোগে রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার কথা ছিল। তাঁর সফরসঙ্গী ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র জাহাজে উঠে পড়েছিলেন, কবির মালপত্রও তাতে তোলা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আকস্মিকভাবে ওইদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে মাদ্রাজ থেকে তাঁর মালপত্র ফিরিয়ে আনা হয়। কলকাতায় কয়েক দিন বিশ্রাম করে ২৪ মার্চ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে আসেন এবং ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে সেখানে বসে ১৮টি গান ও কবিতা রচনা করেন, যা পরে গীতিমালা (১৯১৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়। গীীতমালা-এর ৪ সংখ্যক কবিতা ‘স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি’ যে শিলাইদহে ১৫ চৈত্র ১৩১৮ তারিখ-(২৮ মার্চ ১৯১২) রচিত হয়, তা ওই গ্রন্থে কবিতাটির নিচেই লেখা আছে। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজি গীতাঞ্জলির (১৯১২) সূচনাও হয় এ সময়ে।
আরেকটি হচ্ছে কথায় কথায় অনেকেই বলে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ জমি প্রদান করেছিলেন, অথবা জমি প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। যে কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলো প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং তার বাস্তবায়ন এক জিনিস নয়। সৈয়দ আবুল মকসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রন্থে লিখেছেন- বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হতেই তার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ তাঁদের নবাব এস্টেটের জমি দান করার অঙ্গীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি তাঁদের ৬০০ একর জমি দেওয়ার ঘোষণা দেন। এই বক্তব্য খুব সরল অঙ্কে বিশ্লেষণ করলে যেটা দাঁড়ায় তার অর্থ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ জমি দান করতে অঙ্গীকার করেছিলেন। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রথম সারির মুসলিম নেতা ছিলেন, তবে তিনি কোনো জমি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের জন্য দান করেননি। কারণ স্যার সলিমুল্লাহর পিতা নবাব আহসানউল্লাহ ১৯০১ সালে মারা যান। তারপর সমুদয় সম্পত্তি নবাব আহসানউল্লার আট সন্তান ও তাঁর বিধবা স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। একজন ইংরেজ ম্যানেজার জমিদারি পরিচালনা করতেন। এক সময় নবাব সলিমুল্লাহ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের পারিবারিক কোন্দল তখন চরমে পৌঁছেছিল। ১৯০৫ সালের মে মাসে পুনরায় একজন ইংরেজ সাহেবকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ততদিনে তোষাখানা প্রায় শূন্য। আর ঋণের বোঝাটা উপচে পড়ছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ’র ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ তাঁর জমিদারির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। জমিদারিতে তাঁর অংশ ছিল মাত্র ষোলো ভাগের তিন ভাগেরও কম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার চৌরঙ্গীর বাসভবনে তিনি মারা যান।
নাথান কমিটির রিপোর্টে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি প্রদান প্রসঙ্গে কোনো তথ্য আমার চোখে পড়েনি। রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছিল ১৯১২ সালে। ওই রিপোর্টে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তার সারবক্তব্য হলো-১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্বে ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে যে ক’বছর ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল, তখন রমনায় অনেক খালি জমি ছিল, যেখানে নতুন রাজধানী শহরের অবকাঠামো নির্মিত হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতে ওই স্থানে আরো স্থাপনা নির্মিত হবে বলে বিবেচনাধীন ছিল। সরকারের সম্মত থাকলে সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন-মোটা দাগে ওই মর্মে কমিটি সুপারিশ প্রদান করেছিল। বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এম এ রহিম প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এম এ রহিম তাঁর রচিত গ্রন্থের কোথাও নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে জমি প্রদানের কথা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই মারা যান। ফলে জমি দেবার সুযোগ থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ কথা সবার আগে স্বীকার করতে হবে ঢাকার নবার পরিবারের ভ‚মিকা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতো না। ইতিহাস বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের রাজনৈতিক সামাজিক অংশগ্রহণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক ছিল। ১৯৩০ সাল হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের মধ্যেও রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন ছিল আটটি পর্যায়ে বিভক্ত, যার সময়সীমা ছিল ১৯১৭-১৯৪২ সাল।
লবণ সত্যাগ্রহের (১২ মার্চ, ১৯৩০) মাধ্যমে স্বদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন সে সময় সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করেন। ছাত্রদের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদানের বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন তা ছাত্রদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রীষ্মাবকাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যথারীতি খুললে এখানে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়, যা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আইন অমান্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল পিকেটিং, যেখানে নারীর অংশগ্রহণ এক নতুন মাত্রা আনে। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় পিকেটিং চলার সময় পুলিশ মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করে। পুলিশের তীব্র লাঠিচার্জে বহু সংখ্যক ছাত্র আহত হয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত অজিতনাথ ভট্টাচার্য নামে জগন্নাথ হলের এক ছাত্র শহীদ হয়। উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নি। যাই হোক, আইন অমান্য আন্দোলনে জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলের ছাত্রদের যোগদানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন এবং অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ বহু সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক উপাচার্যের নির্দেশে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে প্রত্যক্ষদর্শীদের লিখিত বক্তব্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিভাত হয় যে ছাত্রদের সাথে নারীও এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।
১৯৩৪ সালের মে মাসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্রী করুণাকণা গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। করুণাকণা গুপ্তা বাংলার বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নৈতিক সমর্থক ছিলেন এবং সম্ভবত তৎকালীন লীলা নাগের নেতৃত্বাধীন ‘শ্রী সংঘ’ ও ‘দিপালী সংঘে’র সাথেও জড়িত হন। ১৯৪১ সালের ১৪ মার্চ হতে ৩ জুন ঢাকায় চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তক্ষয়ী এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয় ‘হোলী’ খেলা দিয়ে। অভিযোগ করা হয় যে বোরখা পরিহিতা একজন মুসলমান মহিলাকে শাখারী বাজারে রঙ দেয়া হয়েছিলো। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও কর্তৃপক্ষের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে নি। তবে জানা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাধারণভাবে ভীতি ছিল এবং ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে কোন কোন স্থানে দাঙ্গাকারীদের দ্বারা নিগৃহীতও হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’ গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘কমনাল হারমনি’ সৃষ্টি করা। আমরা এটা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র ৮৫ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই : “প্রথমে ঠিক হল, একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, যে কোন দলের লোক এতে যোগদান করতে পারবে। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যায় তার চেষ্টা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’। আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে, যাকে ইংরেজীতে বলে ‘কমিউনাল হারমনি’, তার চেষ্টা করা।” [২২] (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃষ্ঠা ৮৫)
১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যদা আদায়ের জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়, যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন শেখ মুজিব। ১১ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই হরতাল প্রথমবারের মতো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাকে নাড়া দেয়। এই হরতাল চলাকালে শেখ মুজিব পুলিশি হামলায় আহত ও গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত: সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাগরণবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ষাটের দশকেও অসাম্প্রদায়িকতার আন্দোলনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল । আওয়ামী লীগের তৎকালীণ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িকতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য তার স্মৃতিচারণমূলক লেখায় অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধুকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে : “১৯৬৪ সালের ১৪ জানুয়ারি। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, সাভার, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দিনকয়েক পূর্বে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের পবিত্র চুল চুরি হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই সময়ে অন্যান্য স্থানের মতো জগন্নাথ হলে দুর্গত নর-নারী-শিশুর জন্য খোলা হয় আশ্রয়শিবির।
সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার ভবনটিসহ বিভিন্ন কক্ষ খালি করে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া হয়। ক্যাম্পের সংগঠন হিসেবে আমি সেদিন পত্রবাহক আখলাখুর রহমানের মাধ্যমে মুজিব ভাই ও মহীউদ্দীন ভাইয়ের কাছে, চাল, ডাল, হ্যাজাক এবং অর্থ প্রার্থনা করি। ছয় ঘণ্টার মধ্যে মুজিব ভাই পাঠান পাঁচ বস্তা চাল, দু-বস্তা ডাল, দুটি হ্যাজাক এবং ২ হাজার টাকা। মহীউদ্দীন ভাই অনুরূপ চাল, ডাল, নগদ অর্থ পাঠান পরের দিন।১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ-সহ প্রধান পত্রিকায় পাঁচ কলামব্যাপী প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম প্রকাশিত হয় ‘পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও’। এক অভিন্ন সম্পাদকীয় কলাম প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয় দাঙ্গা প্রতিরোধের আন্দোলন। সকাল ১০টায় ৩৩ তোপখানা রোড থেকে শুরু হয় বিশাল শান্তি মিছিল। নেতৃত্বদান করেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, মহীউদ্দীন আহমেদ, পীর হাবিবুর রহমান, কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পী কামরুল হাসান, শহীদুল্লা কায়সারসহ অনেকে। মিছিল শেষে নওয়াবপুর রেলগেটের কাছে হাক্কাগুণ্ডা নাগরিক আন্দোলনের নেতা আমির হোসেন চৌধুরীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এছাড়া মহীউদ্দীন ভাই ছুরিসহ এক গুণ্ডাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুজিব ছিলেন জীবন্ত প্রেরণা।”
তিন.
আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরুর সেই সময়টি ছিল বিভাগপূর্ব বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে উত্তাল সময়। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনে তখন সমগ্র বাংলাদেশ খুবই উত্তপ্ত। এ সময় ঢাকা শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অভূতপূর্ব অবনতি ঘটে। পক্ষ তখন দুটি নয়, তিনটি। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে থাকলেও, মুসলমানদের একটি পক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার বিরোধী। যদিও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস-কর্মীদের জোর ও সাংগঠনিক তৎপরতা বেশি, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী পক্ষও দুর্বল ছিল না। ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ প্রথমে ছিলেন দোদুল্যমান, পরে আন্দোলনের বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন তিনি সমর্থন করেননি।
১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। তবে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি যতটা আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে হতে পারত, তা হয়নি। সেদিনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি ছিল আনন্দ ও বেদনায় মিশ্রিত। পূর্ব বাংলার ও ঢাকার গণমান্য ব্যক্তিদের অনেকেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধানত সরকারি কর্মকর্তারাই কার্জন হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক বিশিষ্ট হিন্দু নেতা যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এক অনাড়ম্বর কিন্তু ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নবাব হাবিবুল্লাহ।
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী এ সময় লেখাপড়া ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভে অংশ নিয়ে কারাবরণ করছিলেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ঢাকার হিন্দু-মুসলমান বহু নেতা কারাভোগ করেন। এমনকি রাজভক্ত ঢাকার নবাব পরিবারেরও কেউ কেউ কারাবরণ করেন। যেমন খাজা আবদুল বারী, খাজা সোলায়মান কদর, আবদুস শাকুর, জিন্দাবাহারের জমিদার চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, তাঁর ভাই চৌধুরী সেলিম জেলানী প্রমুখ। ঢাকা জেলা কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী), জেলা কংগ্রেস সভাপতি অতুলচন্দ্র সেন, চন্দ্রকান্ত বেদান্তকান্তী, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তখন অন্তরীণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকার হিন্দু ও মুসলমান নেতারা অনেকেই যোগ দিতে পারেননি। ‘বন্দে মাতরম’ ও ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিতে তখন ঢাকার প্রতিটি পাড়া-মহল্লা মুখরিত। সর্বভারতীয় নেতারা এ সময় ঢাকা সফর করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ওপর জোর দেন।
১৯২০ সালের ১৮ মার্চ করোনেশন পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু-মুসলমানের মিলনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করতে হবে।’ যদিও বাস্তবে সেই বন্ধুত্ব হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের আন্দোলন থেকে নবাব হাবিবুল্লাহ ও এ কে ফজলুল হক নিজেদের সরিয়ে নেন। ফজলুল হক বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলমানরা, কারণ তারা এমনিতেই রয়েছে পিছিয়ে। এভাবে লেখাপড়া ফেলে রাজপথে আন্দোলন করলে এবং সে জন্য কারাভোগ করলে মুসলমানরা আরও পিছিয়ে পড়বে; শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, চাকরি-বাকরিসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে। পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা প্রায়ই বলা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুরু থেকেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পূর্ব বাংলার সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ উপকৃত হয়েছে। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে গ্রামীণ মুসলমান মধ্যবিত্ত, সম্পন্ন কৃষক ও নিন্মবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে ২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলায় একটি নতুন হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়, যারা শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশকের মধ্যে পূর্ব বাংলায় একটি আলোকিত আধুনিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।
চার.
১৯২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন চব্বিশ পরগণা জেলার মহামেডান এসোসিয়েশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে বিরোধিতা করেছিল। মওলানা মুহাম্মদ আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর মওলানা আকরাম খাঁ বলেছিলেন, মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা স্কুলই বেশি প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে কলকাতার সুশীল সমাজের পক্ষে যাঁরা নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেতা ড. রাসবিহারী ঘোষ ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা প্রদেশ ভাঙনের মুখে পড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন কলকাতার স্বনামধন্য আইনজীবী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ঢাকার কেউ কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিলেন না?
জানা যাচ্ছে যে, সে সময় ঢাকা কংগ্রেস সমর্থিত একটি বড় সামাজিক সংগঠন ছিল। তার নাম পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানটি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে বিরোধিতা করেছিল। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হার্টগের বিরুদ্ধে জঘন্য সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার তারা চালিয়েছিল। সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন-নোংরামির একটি দৃষ্টান্ত হলো, ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষের বিষয়টিও টেনে আনা হয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ প্রচারণা চালাতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর পেছনে কারসাজি হলো তিন ইহুদির। সেই তিন ইহুদি হলেন উপাচার্য হার্টগ, গভর্নর জেনারেল লর্ড রিডিং এবং ভারত সচিব ই মন্টেগু। ঢাকা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের একজন আইনজীবী এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের পক্ষে পূর্ণপ্রাণেই সম্পৃক্ত ছিলেন। আশুতোষ মুখার্জি যখন বুঝলেন প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধা প্রদান করে কোনো লাভ হবে না, তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট তৎপর হন।
১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এ কারণে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করেন। তিনি বেসরকারিভাবে তহবিল সংগ্রহের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সরকার প্রথমদিকে আশুতোষ মুখার্জির এইসব তৎপরতায় সায় দিলেও পরে তাতে ভাটা পড়ে। আশুতোষ মুখার্জির কর্মকান্ডের প্রতি বিরক্ত সরকারের তরফ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে তাঁর কার্যকলাপের প্রতি সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ। তিনি ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করেন। এইসব কর্মকান্ড থেকে প্রতীয়মান হয় প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে জ্ঞান ঘোষের নিয়োগ প্রদানকে কেন্দ্র করে। জ্ঞান ঘোষ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার অল্প আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিষয়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জির মতো উদার ব্যক্তিত্ব যে কাজটি করেছিলেন সে সম্বন্ধে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেছিলেন- জ্ঞান ঘোষ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন-সেখানে তিনি রিসার্চ করতেন। তার বোধ হয় শর্ত ছিল রিসার্চ ছেড়ে চাকরি নিলে টাকা ফেরত দিতে হবে। এটা স্যার আশুতোষ মাফও করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। জ্ঞান ঘোষকে ঢাকায় আসার মাশুল দিতে হলো। স্যার আশুতোষ মেড হিম পে দি ফুল সাম; দশ হাজার টাকাই তাকে দিতে হয়েছিল।...সেন্ট্রাল লেজিসলেচার-এর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটটা ইনটারেস্টিং। ওই ডিবেটটা দেখলেই হয়। জ্ঞান ঘোষ ২৯ বছর বয়সে পুরো প্রফেসর হন। হি ওয়াজ প্রবাবলি দি ইয়ংগেস্ট প্রফেসর। তিনি কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। জ্ঞান ঘোষ, সত্যেন বোস- এঁরা এক ব্যাচের। এই সব ঘটনা এবং তার প্রবাহ দেখলে মনে হয়-বাংলার অতীত ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমন মোহনীয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে খুব নির্মম।
পাঁচ.
এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ১৯৪১ সালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল মারাত্মক। এর ফলে অনিবার্যভাবে ঢাকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঙ্গার সময় পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল না-যা এই দাঙ্গা সম্পর্কিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা এতই মারাত্মক ছিল যে ছাত্রী নিবাসের সুপারিনটেনডেন্ট চারুপমা বসু উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাসস্থান সুরক্ষার প্রয়োজনের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়ন বা ছাত্রী পরিষদের বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয় কার্জন হলে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নবগঠিত ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পূর্বে প্রচলিত নিয়মানুসারে মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয় একটি ‘মঙ্গল ঘাট’। অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম্’ এর মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে ‘বন্দে মাতরম্’ ইতোমধ্যে পরিণত হয়েছিল এক সর্বভারতীয় ঐক্য গীতিতে। ঢাকা হতে প্রকাশিত সমসাময়িক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ বিষয়ে ‘বন্দে মাতরম্ গানে বিপত্তি’
শিরোনামে নিন্মোক্ত তথ্য পরিবেশিত হয়:
‘গত ৩১ শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত গীত হয়। প্রায় ১০ মিনিট কাল পরে একজন মুসলমান ছাত্র ভাইস-চ্যান্সেলার ডা: হাসানকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন ‘বন্দে মাতরম্’ গান করিবার অনুমতি দিলেন? মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় ছাত্রটিকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলেন, ‘‘এটি ছাত্রীদের অনুষ্ঠান, সুতরাং আগে ইহার কার্য্য শেষ হউক, পরে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে’’। কিন্তু বাধাদানকারী ছাত্রটি জিদ্ করিতেই লাগিলেন। তখন সমবেত ছাত্রগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভাইস-চ্যান্সেলরের উপস্থিতিতেই বচসা আরম্ভ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে চেয়ার ছুড়িয়া মারিতে থাকে। ক্রমে হলের বাহিরেও হাঙ্গামা বিস্তৃত হয় এবং হকি স্টিক ও সোডার বোতল বেপরোয়া চলিতে থাকে। ভাইস চ্যান্সেলার দাঙ্গা থামাইবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি অকৃতকার্য হন। পরে সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করে। আহত ছাত্রদের মধ্যে তিন জনকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। ঐ দিন সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে পাহারা দেয়। ’
৩১ শে জানুয়ারী তারিখে কার্জ্জন হলে উইমেন্স ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভাইস চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করা হয় নাই। কিন্তু পরে একজন মুসলমান (সম্ভবতঃ ছাত্র) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে যে পূর্ব্ববর্তী বৎসরের অধিবেশনে ডাঃ মজুমদার ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত গীত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন এই বৎসর এইরূপ করা হইল। ভাইস-চ্যান্সেলার বলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জানেন না এবং এই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। প্রশ্নকর্ত্তা এই উত্তরে অসন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করে এবং বিশৃংখলার মধ্যে সভা ভাঙ্গিয়া যায়।
এই ঘটনায় ১৬ জন ছাত্র আহত হয়, যাদের মধ্যে ৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান। আহতদের মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র নাজির আহমদ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অতীব মর্মান্তিক। পাঠকবর্গ অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বৃটিশ বিরোধী ভূমিকার জন্য অজিত নাথ ভট্টাচার্য প্রাণ বিসর্জন দেন, আর ১৯৪৩ সালে ঔপনিবেশিক শক্তি সৃষ্টি-রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন নজীর আহমদ। উভয় ঘটনার উৎস স্থল একই। যাই হোক, এই ঘটনার সময় অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় কিছু সংখ্যক ছাত্রী লাঞ্ছিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এটিই ছিল প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৩ সালের এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পর অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মারাত্মকভাবে চিন্তিত করে তোলে। জরুরী ভিত্তিতে ৩ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ অবিনাশী, কোন ভাবে একবার জাগ্রত হলে সহজে নিবারণ করা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কে ‘ঢাকা প্রকাশ’ সংবাদ পরিবেশন করে: মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের সকল স্কুল ও কলেজ বন্ধ ছিল। এই দিন প্রাতে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। তাহারা জনসাধারণকে আত্মঘাতী ভাতৃবন্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ জানায়। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণ পুনরায় এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের নিকট যে কোন উপায়ে পারস্পরিক হানাহানির অবসান ঘটাইয়া ঢাকা নগরীর লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবেদন জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মোটর চড়িয়া শোভাযাত্রীদের সহিত পরিভ্রমণ করেন। ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় উদ্যম নাগরিকদের মনে আস্থার সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৈনন্দিন কাজকর্ম অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে।
১৯৪৭ সালের দাঙ্গার প্রভাব বহুদিন বিদ্যমান ছিল। এই দাঙ্গার পর পরই পূর্ব বাংলা হতে বহু সংখ্যক হিন্দু ভারতে অভিবাসী হতে শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে চলে। পূর্ব বাংলার অধিবাসী হিন্দুদের উদ্বাস্তু হিসেবে ভারত গমনের সময়ও তাঁদের উপর অত্যাচার চলে। ১৯৪৮ সালে এরই প্রতিবাদ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীদ্বয়ের একজন বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগ। এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে অভিবাসন হয় পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলা হতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে যেখানে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ছিল (নতুন ভর্তি) ৪৩ জন, ১৯৪৯-৫০ শিক্ষাবর্ষে তা হয়ে যায় মাত্র ২ জন। ১৯৫০ সালের পর বেশ কিছু দিন কোন হিন্দু ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়নি। ১৯৫০ সাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আবার শুরু হলো। প্রথম ঘটনা ঘটে খুলনার কালিশিরা গ্রামে। তারপর ছড়িয়ে পরে বরিশাল, ফরিদপুর ও ঢাকায়। প্রতিশোধ হিসেবে কলিকাতায় ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সূচিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই দাঙ্গা ছিল স্মরণ কালের মধ্যে ভয়াবহতম। পরিস্??