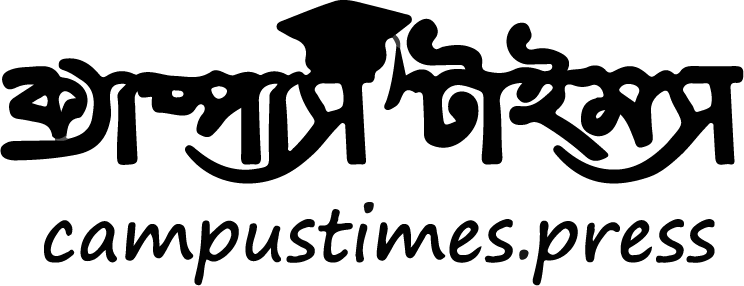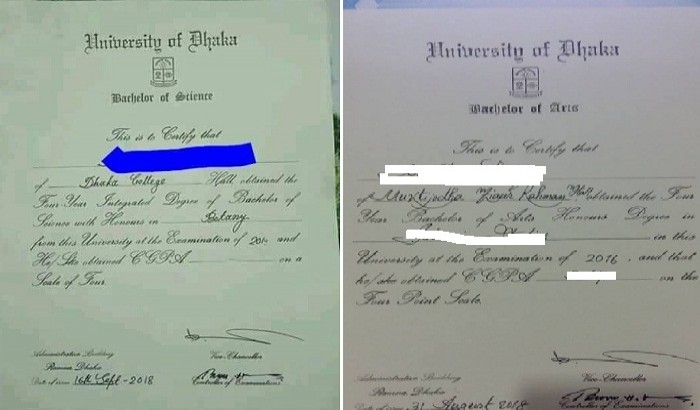|| সহস্র সুমন ||
আমেরিকার মিনিসোটা রাজ্যে মিনিয়াপোলিস শহরের নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকান্ডটিকে বর্ণবাদের চশমায় দেখা হচ্ছে কেন এটি নিয়েই একটা প্রশ্ন হতে পারতো। ‘একজন নাগরিক খুন হয়েছেন পুলিশের হাতে’, বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে লম্বা স্টেটমেন্টের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে এই ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ উপর্যুপরি ঘটতে থাকে, তখন বিষয়টি আর কেবল নাগরিক হত্যার বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন তা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক, নৃ-তাত্তি¡ক ও আত্মকেন্দ্রীক। জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার যে সিসিটিভি ভিডিওটি নিউইয়র্ক টাইমস এর পেজ-এ প্রকাশ করা হয়েছে সেটি বেশ কয়েকবার দেখলাম। একটি ফ্রড বিলিং এর অভিযোগে পুলিশের দুটি গাড়ি এসে তাকে ধরে ফেলে। এই অভিযানে পুলিশ অফিসার শেভলিন ডেরেক মুখ্য ভূমিকা পালন করে যিনি কিনা আমেরিকার পুলিশ আইন কর্তৃক সমর্থিত ও বহুল ব্যবহৃত এরেস্ট করার পদ্ধতি ‘নি টু নেক’ ব্যবহার করেন। প্রায় আট মিনিটের বেশি সময় ধরে তার ঘাড়ে হাঁটু চেপে ধরে রাখলে ফ্লয়েড কয়েকবার বলেছে ‘আমি শ্বাস নিতে পারছি না’। তবুও তাকে রিলিজ করা হয় নি। জর্জ ফ্লয়েড একজন মানুষ হয়ে অন্য একজন মানুষের হাঁটুর নিচে প্রাণ দিয়ে দিলেন। আমেরিকার ইতিহাসে বর্ণবাদ বিরোধী নতুন এক আন্দোলন শুরু হলো- ‘বø্যাক লাইভস ম্যাটার’। এই আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী বিপুল সমর্থন পেয়েছে এটা সত্য কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, নিই ইয়র্ক, মিনিসোটার বিভিন্ন স্টোর লুটপাটের ঘটনা খুব সহজেই আন্দোলনকারী ও কালো নাগরিকদের আচরণকে বিতর্কিত করে ফেলেছে পরমুহূর্তেই। বর্ণবাদ আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষদের একটি মনজাগতিক বিষয় যা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে ব্যাপক প্রভাবিত করে। বর্ণবাদের তত্ত¡ কথা ছাড়াও আমার নিজের দু চারটে অভিজ্ঞতার আলোকে জর্জ ফ্লয়েডের থার্ড গ্রেড হত্যাকান্ডটিকে ব্যাখ্যা করব এবং বর্ণবাদের কাঠামোটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ঘটনাটি আমেরিকায় ঘটলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় দু জায়গাতেই কালো নাগরিকদের প্রতি সাদা নাগরিক ও শাসক শ্রেণির প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম উদাহরণটি দিতে চাই জার্মানি থেকে।
গত বছর জার্মানির হামবার্গ শহরের ফ্রেসব্রডল নর্ড নামক একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসেছি। ঝকঝকে ট্রেন, চকচকে মানুষগুলো। ছোট ছোট ফর্সা শিশুরা ফর্সা ফর্সা মায়েদের সাথে আমুদে খেলা খেলছে। একটু দূরে একজন শ্যামলা ভদ্র লোককেও দেখলাম বসে আছে। তার পাশের সিটটা খালি। আমি আসলে প্রথমে বিষয়টাকে অন্যভাবে চিন্তা করি নি। একটা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়ালে বেশ কিছু লোক উঠলো। সে সময় এক ফর্সা রমনী উঠলো আমাদের কামরায়। মেয়েটি বসার সিট খুঁজছিল এবং দেখলো যে দুটো মাত্র ছিট খালি। সে আমার পাশেই বসে পড়ল। কিন্তু অবাক ব্যাপার ঘটল ঠিক পরের স্টেশনে। আমার সামনের একটা আসনের সাদা যাত্রী নেমে গেলেন এবং আমার পাশের নারীটি সেই সিটে গিয়ে বসলেন। সেই সিটের পাশের সিটগুলোতে সবাই সাদা ছিলেন। আমি ভীষণ অবাক হলাম। আমি এও লক্ষ করলাম যে সেই শ্যামলা ছেলেটি এই ঘটনা দেখে মুচকি হাসছে। এর মানে হলো সে বিষয়টি বুঝতে পেরেছে যে আমি আসলে তাদের গোত্রের নই জন্য মেয়েটি সিট বদলে নিলো, ঠিক যে কারণে তার পাশে কেউ বসে নি। তবে মেয়েটি কেন প্রথমে আমার পাশে বসেছিল, কেন ঐ ছেলেটির পাশে নয়? এর কারণও আমার কাছে বেশ পরিষ্কার। সেটি হলো আমি ঐ ছেলেটির চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেকটা ফর্সা ছিলাম। ঘটনাটি আমি অনেক দিন মনে রাখবো, সম্ভবত যত দিন বাঁচবো তত দিন। এটা বললাম রঙের কারণে কি বৈষম্য হতে পারে তার একটি আচরণগত দিক। ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকেও যেতে হবে আমাদের এবং এ জন্য প্রয়োজন হবে নিরেট তথ্য এবং তাত্তি¡ক আলোচনার। এর আগে ভিন্ন কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক। কালো নাগরিকদের বিষয়ে আপাতভাবে আমাদের কি ধারণা? অনেকে বলতে পারেন, আমাদের ধারণা দিয়ে কি যায়-আসে? আসলে যায়-আসে। ধারণা বিশ্বাসের জন্ম দেয়, সেই বিশ্বাস একটি সংস্কৃতিতে রূপ নেয় এবং এভাবেই আসে একটি আইন। রূপান্তর একটি বাস্তব এবং সত্য প্রক্রিয়া।
ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি প্রচলিত ধারণা হলো, কালো নাগরিকগণ নৈতিকভাবে দূর্বল, উগ্র এবং অপরাধপ্রবণ। এটি যে কেবলই একটি ধারণা তাও নয়। কেননা একটি গবেষণায় দেখা গেছে ইউরোপে যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে প্রতি বছর তার সিংহভাগ করছে কালো এই নাগরিকেরা। কথা যে একেবারে মিথ্যে তা নয়। কিন্তু সাদারাও কি করছে না? সাদারাও কি তাদের অপরাধ কার্যক্রমে কালোদের ব্যবহার করছে না? কোনটি অপরাধ এবং কোনটি অপরাধ নয় সেই বিচারে সাদা সাসপেক্ট কি একটু বেশি প্রিভিলেজ্ড নয়? কালোকে দেখা মাত্রই এটা পুলিশের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে সে অপরাধী। জার্মানির যে ঘটনাটি বললাম ঠিক তার এক মাস পরের ঘটনা। আমি প্যারিসের একটি রেল স্ট্রেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আপনারা যারা ফ্রান্স থাকেন বা গিয়েছেন তারা জানেন যে ফ্রান্সে প্রচুর কালো নাগরিক কারণ আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। সেই সূত্রে কালো লোকগুলো ফ্রেন্স ভাষা ভালো জানে এবং ফ্রান্সে তাদের প্রবেশ করা বেশ সহজ। আমি দেখলাম একটা করে ট্রেন আসলে একটা কালো তরুণ গেটের কাছে ছুটে যায় ট্রেনে ওঠার জন্য। ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করার পর সে আবার ফিরে আসে এবং একটা বেঞ্চে বসে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পরের ট্রেনের বিষয়েও একই অবস্থা। সে ভিড়ের মধ্যে যায়, ঠেলাঠেলি করে কিন্তু ওঠে না। আমার বন্ধু যে কিনা প্যারিসে প্রায় সাত বছর ধরে থাকে, তাকে আমি প্রশ্ন করলাম এ বিষয়ে। সে জানালো, ‘এরা পকেট মারে’ এবং ফ্রেঞ্চ পুলিশ এদের নিয়ে বিরক্ত। পুলিশে ধরলেও কিছুক্ষণ পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। ট্রেন স্টেশনে সব সময় পকেট পিকিং ও ফ্রডের বিষয়ে এনাউন্সমেন্ট দেয়া হচ্ছে। এরপর আমি যে কদিন প্যারিসে ছিলাম কালোদের আচার আচরণ লক্ষ করার চেষ্টা করেছি। আইফেল টাওয়ারের পাশে প্রচুর স্ট্রিট সেলার ও ভ্যাগাবন্ড টাইপ কালো নাগরিক দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ তারা বেশ লাউড, ট্রেনের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলে, হুড়োহুড়ি করে ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো সাদাদের মধ্যে একটা পারসেপশন তৈরী করেছে যে, কালোরা আসলে সম্পুর্ণ সভ্য নয় বা তাদের কাতারের নয়। এই পারসেপশন খুবই ভয়ংকর, প্রত্যেকটি প্রজন্ম যদি এমন একটি ধারণা নিয়ে বড় হয় যে কালোরা ইনডিসেন্ট, মুসলিমরা টেরোরিটস্ট এবং চায়নিজরা ভাইরাস ছড়ায় তখন বৈষম্যমূলক আচরণগুলো এক ধরণের ডি ফ্যাক্টো বৈধতা পেয়ে যায়। আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন অপরাধ তদন্ত সংস্থার রিপোর্ট থেকে দেখা যায় সাদাদের চেয়ে কালো নাগরিকেরা কম জামিন পায়, কঠোর শাস্তি পায়, বেশি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া ক্রাইম এন্ড রেইস বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাতেও দেখা গিয়েছে যে কালো নাগরিকরা এমন একটি আর্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে যে তারা খুব সহজেই অপরাধী হয়ে উঠতে পারে, বা তাদের খুব সহজেই অপরাধী মনে করা যেতে পারে।
সেন্ট্রাল লন্ডনে মধ্যরাতে শত শত কালো নাগরিককে মদ্যপ অবস্থায় চিৎকার করতে করতে হাটতে দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় ফ্রড বিলিং করতে যত নাগরিককে দেখা যায় তার একটা বড় অংশ কালো নাগরিক। এই বিবৃতিগুলো কিন্তু কালোদের প্রতি আমাদের সবারই একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে যথেষ্ট। কিন্তু একটু ভেবে দেখি, চাকরিতে কালোদের এক্সেস কম। বলা হয় আমেরিকাতে একটি ফার্মে একজন সাদা সারনেমের ব্যক্তি ও একজন কালো সারনেমের ব্যক্তি যদি এক সাথে আবেদন করে তাহলে সাদা লোকটি কালো লোকটির চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ এগিয়ে থাকবে। কালো নারী সাংবাদিক খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে কয়েকবার। সে দেশে সাদা ও কালোদের জন্য এক সময় আলাদা আলাদা টয়লেট, বাস, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সমাজের মধ্যে বৈষম্য খুঁজি আমরা। সামাজিক বিজ্ঞানে গড়ে তুলি রেসিজম, ইন্টারসেকশনালিটি, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু মানুষের মগজের মধ্যে যে বিশ্বাসের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে সে খবরও আমাদের নিতে হবে। কালোদের একটি দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বৈষম্যের দুষ্ট চক্রের মধ্যে থেকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না। ফ্রড বা চুরির মতো কাজগুলো তারা তখনই করে যখন তাদের ডিসেন্ট ওয়ার্ক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, বৈষম্য করা হয়। সেই বৈষম্যের কারণে তারা মেন্টাল ইনফেরিওর স্টেজ থেকে বের হতে পারে না। তারা নিজেদের মূল ধারায় নিয়ে আসতে চাওয়ার ক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পরে; বঞ্চিত হওয়ার আতঙ্ক, অপমানিত হওয়ার আতঙ্ক।
যারা আমেরিকার রেসিজম বিষয়ে একটু মানবীক ধারণা চান তারা দুটো মুভি দেখতে পারেন। একটি হলো ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন পরিচালিত ‘জাস্ট মারসি’। আলাবামা স্টেটের ১৯৮৬ সালের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এই চলচিত্রে দেখানো হয় কিভাবে ‘কালো মানুষ মানেই অপরাধী এবং অপরাধী মানেই কালো মানুষ’ ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করেছিল সে সময়। একজন সাদা ক্রিমিনালের মার্ডার চার্জটি কত সহজেই একজন কালো আফ্রিকান আমেরিকান জনি ডি এর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া গিয়েছিল। তবে সে যুদ্ধে জনি ডি হেরে যায় নি। একই ভাবে হেরে গিয়েছিল না ক্যাথরিন জনসন ‘হিডেন ফিগার’ চলচিত্রের মধ্যেও। থিওডর মেলফি পরিচালিত ‘হিডেন ফিগার’ কালো নারীদের বৈষম্যের উপাখ্যান। আমেরিকার নাসাতে ষাটের দশকে নারীদের সাথে কি আচরণ করা হতো এবং সেই নারী যদি কালো বা নিগ্রো হতো তাহলে তার কপালে কি অপমান জুটতো এই ইন্টারসেকশনালিটির চিত্র খুঁজে পাবেন এই চলচিত্রে। যদিও ক্যাথরিন জনসন নামের সেই নিগ্রো নারীর কারণেই আমেরিকার আকাশে প্রথম মনুষ্যবাহী রকেটের উৎক্ষেপণ হয়, চাঁদে প্রথম মার্কিনিরাই পা রাখে। আজ সেই পা চেপে ধরেছে জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়।
মার্টিন লুথার কিং তার পিটার্সবার্গ ভাষণে বলেছিলেন, ‘আমি সেই আমেরিকার স্বপ্ন দেখি যেখানে সাদা ও কালোর মধ্যে কোন তফাত থাকবে না।’ তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এখনও অনেক দূর হাটতে হবে আমাদের। মার্টিন লুথার কিংকে আসতে হবে কালে-কালে, দেশে-দেশে। বর্ণবাদ কোন একটি দেশ বা একটি কালের সমস্যা নয়। এটি যুগে যুগে, দেশে দেশে বর্তমান। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের বর্ণবাদের শিকার যারা তাদের চোখে পৃথিবীকে দেখতে হবে। যেদিন সেই জার্মান নারী আমার পাশের সিট থেকে উঠে চলে গিয়েছিল সেদিন সামান্য হলেও বুঝেছিলাম বর্ণবাদের মানে কি! যখন মুসলিম শুনলেই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সাদারাই সিরিয়া বা আফগানিস্থানের প্রসঙ্গ তোলে তখন বুঝি বর্ণবাদের মানে কি! আমরাও স্বপ্ন দেখি যেদিন বর্ণবাদ থাকবে না, আঞ্চলিকতাবাদ থাকবে না। এই পৃথিবীতে কোন ফ্লয়েড, সে হোক কালো বা সাদা, আর পুলিশের হাঁটুর নিচে প্রাণ দেবে না। কোন বিচারপ্রার্থি বিক্ষুব্ধ জনতা বিচার চাওয়ার নামে শহরের দোকানপাট লুটপাট করবে না। আর কোন চাকুরী প্রার্থীর সারনেম দেখেই ধারণা করা হবে না তার গায়ের রং, তার বংশ পরিচয়। আগেই নির্ধারিত হবে না কে এই চাকুরীর জন্য বেশি যোগ্য হবে বা কে বেশি পারিশ্রমিক পাবে। তাহলেই সব রং মুছে মানুষ পরিণত হবে মানুষে।
সহস্র সুমন
লেখক ও কবি
পাবলিক পলিসি গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার, যুক্তরাজ্য